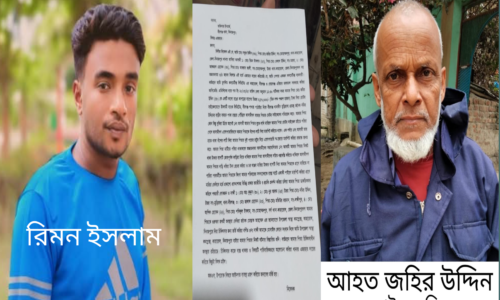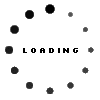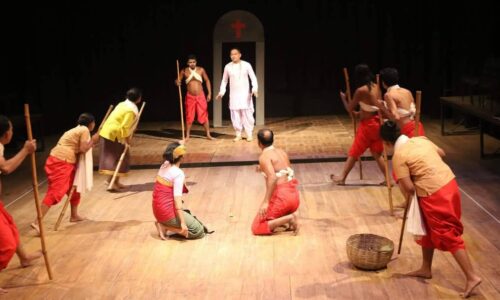প্রতিনিধি 10 December 2024 , 2:58:25 প্রিন্ট সংস্করণ
জেমস আব্দুর রহিম রানা:

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর পালিত হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার এবং মর্যাদা সুরক্ষার জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকারকে নির্দিষ্ট করে সেসব বাস্তবায়নের জন্যই রাষ্ট্রগুলো এ মানবাধিকার সনদ গ্রহণ করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনে মানবাধিকার সনদের এ ঘোষণাপত্র প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রগুলোকে দেশীয় আইনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাতে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি না করলেও অত্র দলিলটিতে সব রাষ্ট্রের সম্মিলিত সমর্থন থাকার ফলে বিশেষজ্ঞরা এটিকে প্রকারান্তে আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের অংশ হিসেবে মনে করেন। পরবর্তী সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের ফলে বিশ্ব বিভাজনের প্রভাব মানবাধিকারেও লক্ষণীয় ছিল। যেমন পশ্চিমা বিশ্ব তখন থেকেই রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিত আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্ররা মানবাধিকার বলতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত। এর ফলে প্রায় ১৮ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে দুটো আন্তর্জাতিক চুক্তি গৃহীত হয়েছিল জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যার একটিতে ছিল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার এবং অন্যটিতে ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলত এ দেশে মানবাধিকার চর্চার নিশ্চয়তা পাওয়ার প্রচেষ্টা ছিল এবং প্রাথমিক সফলতা অর্জন হয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলো মানবাধিকারকে এ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সোভিয়েত সমর্থক দেশ হলেও বাংলাদেশ মূলত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছিল কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি বরং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত যেকোনো অধিকারের যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে নাগরিকরা উচ্চ আদালতে প্রতিকার চাইতে পারে যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ মূলনীতিগুলো নাগরিককে সঠিকভাবে দিতে না পারলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে কোনো ধরনের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকে না। মানবাধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তানো আছে রাষ্ট্রের ওপর এবং এ অধিকারগুলো থাকে জনগণের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করে যথাযথ সুরক্ষা দেয়া। স্বাধীন বাংলাদেশ ৫০ বছর অতিক্রম করার পরও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করার যথেষ্ট সময় এবং উপযোগ বিদ্যমান।
প্রথমত, বাংলাদেশ উল্লিখিত দুটো মানবাধিকার দলিলেই অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র। এ দুটি ছাড়াও বাংলাদেশ শিশুদের অধিকার, নারীর অধিকার, বর্ণবৈষম্য, নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মানবাধিকার দলিলে অনুসমর্থনকারী দেশ। ফলে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যবাধকতা রয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোয় উল্লেখিত অধিকারগুলো দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকসহ সবার জন্য নিশ্চিত করা এবং এ লক্ষ্যে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা। বেশ কয়েকটি অধিকার সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা অতীব জরুরি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ চিকিৎসা, বাসস্থান এবং শিক্ষার অধিকার সরাসরি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করতে সামর্থ্য রাখে। আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন নিরাপত্তার এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকা এবং সহজে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকা জরুরি। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিনা বিচারে আটক, পুলিশ তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় মৃত্যু, রিমান্ড নির্যাতন, হয়রানি, হুমকিসহ বিভিন্ন মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন ৫০ জন কর্মীর নিরাপত্তার বিষয়ে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ চার মাস গবেষণা করে ফলাফল জানায় যে মানবাধিকার কর্মীরা গুম, আইনি হয়রানি, শারীরিক আক্রমণ, ঘুস এবং কাজের বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট গত আগস্টে বাংলাদেশ সফরকালে ‘বলপূর্বক গুম ও বিচার-বহির্ভূত হত্যার অভিযোগ তদন্ত’ করার জন্য সরকারকে একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। কাজেই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা প্রদানে রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বাগ্রে।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত দেশীয় আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে যেমনটা ইংল্যান্ডে মানবাধিকার আইন নামে নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। অথবা বৈষম্য বিরোধ আইন নামে সংসদ নতুন আইন তৈরি করতে পারে যেটি পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশেই আছে।
বাংলাদেশের উচ্চ আদালতই যেহেতু সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো জনগণকে নিশ্চিতভাবে উপভোগের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে একমাত্র প্রতিকার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রকে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দিতে পারেন। উচ্চ আদালতের মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার বেশির ভাগই রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অথবা আইন অনুযায়ী নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায়ই লঙ্ঘনীয় হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈষম্যের শিকার হওয়া একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে টেকনাফ বা তেঁতুলিয়া থেকে সাংবিধানিক অধিকারকে বলবৎ করতে ঢাকায় উচ্চ আদালতে এসে সময়-শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে কতটুকু সফল হতে পারে তা ভাবনার বিষয়। এছাড়া বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে অনুসমর্থন দিয়েছে সেগুলোর সংশ্লিষ্ট কোনো অধিকারের প্রশ্ন উচ্চ আদালতে উত্থাপিত হলে তা উদারতার সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডকে গুরুত্ব দিতে পারে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখিত অধিকারগুলোর একটা বড় অংশই বাংলাদেশের জনগণ যথাযথভাবে উপভোগ করার সুযোগ পাবে। উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সনদগুলোয় বাংলাদেশের অনুসমর্থন থাকা সত্ত্বেও দেশীয় আইনের বিধানকে গুরুত্ব দিয়েছে অথবা দেশীয় আইনের অনুপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অধিকারগুলোকে সরাসরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। তবে আশার জায়গা হচ্ছে, বাংলাদেশের উচ্চ আদালত দেশীয় আইনের অনুপস্থিতিতে কোনো আইনগত সমস্যার সমাধানকল্পে সহায়ক হিসেবে ব্যাখা-বিশ্লেষণের সময় আন্তর্জাতিক মানবাধিকারগুলোকে বিবেচনায় নিতে পারে এমন মতামত ব্যক্ত করেছে বেশ কয়েকটি মামলায়।
এটা বলা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারগুলো সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে পারে এমনটা কেউই নিশ্চিত করতে পারবে না। এসব অধিকারের বিষয়েও আলোচনা এবং সমালোচনা রয়েছে যে এগুলো পশ্চিমা বিশ্বের তৈরি এবং ওই সমাজের জন্য প্রযোজ্য। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিন্নতা এবং স্বকীয়তাকে বিবেচনা করে প্রয়োজন। যেমন প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা আসলে পশ্চিমা বিশ্বে আর আমাদের অঞ্চলে ভিন্নতা রয়েছে। তার পরও যেহেতু বাংলাদেশ ওইসব চুক্তিকে অনুসমর্থন করেছে, তাই আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে যাতে করে আমাদের জনগণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক জীবন ব্যবস্থার সুরক্ষা মর্যাদাসহকারে নিশ্চিত থাকে। একই সঙ্গে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে সেগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক আচরণের একটা বড় অংশই নির্ভর করে ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের ওপর। কোথাও দাড়ি-টুপি বা হিজাব-নিকাবের কারণে বৈষম্যের নজির যেমন আছে তেমনি টিপ পরা বা একটু ভিন্নভাবে পোশাক পরিধানের ফলেও বৈষম্যের শিকার হওয়ার নজির আছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হয়। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত ও গভীরভাবে গবেষণার প্রয়োজন।
বাংলাদেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং যথাযথ সুরক্ষার জন্য সর্বজনীন ব্যবস্থাপনায় উপরোল্লেখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেয়া দরকার বলে মনে করি। মানবাধিকার নিশ্চিত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেটির নিশ্চয়তা কেবল জনগণের উপভোগের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। শুধু লিখিত আইন করলেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয় না বরং শুরু হয়। আইনগুলো কতটুকু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখতে হবে। এছাড়া জনগণ বিভিন্নভাবে কতটা নিরাপদ, তাদের জীবনযাত্রা কতটা মানসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ তাদের সঙ্গে কতটা সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে সেবা প্রদান করে থাকে, সেসবের ভিত্তিতেই নির্ধারণ হয়ে থাকে মানবাধিকার চর্চার মাপকাঠি। মতের ভিন্নতার কারণে হয়রানি করার ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সদাচরণ এবং আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সময়মতো যথাযথ প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা জনজীবনে মানবাধিকারের সুফলতা দিতে পারে।
মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে অবিভাজ্য এবং পরস্পর সম্পর্কিত মানবাধিকারগুলো অনেকটা মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো থাকার ফলে কিছু অধিকার নিশ্চিত করলেই রাষ্ট্র জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। যেমন শিক্ষার অধিকার না থাকলে বা পরিবেশের অধিকার না থাকলে সে অর্থে জীবনের অধিকার নিশ্চিত হয় না। আবার নিরাপত্তার অধিকার এবং বৈষম্য নির্মূলের ব্যবস্থা না থাকলে কোনো অধিকার যথাযথভাবে উপভোগ করা অসম্ভব। কাজেই প্রয়োজন হলো প্রতিটি মৌলিক অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করা। অন্তত এ বছর মানবাধিকার দিবসে এটাই হোক প্রত্যাশা।