
রাষ্ট্র ভাষা বাংলার আদি অন্ত আবু তালহা বিন মনির
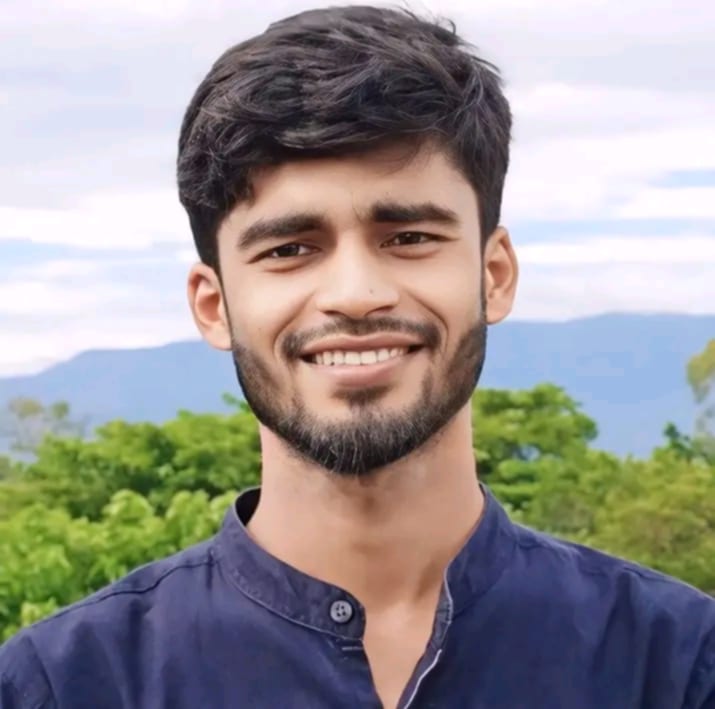 আবু তালহা বিন মনির
আবু তালহা বিন মনির
ভাষা,জাতি সত্তা পরিচয়ের প্রধান বাহক।লোকের মায়ের ভাষা দিয়ে আমরা তার জাত,তার জাতি সত্তার পরিচয় বের করে নিতে পারি।গত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "স্বাধীনতা ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম- "ভাষা,স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড।একটি জাতির প্রধান উপজীব্য।" ভাষাই মনুষ্য জাতির প্রধান অধিকার।আর সেটা মাতৃভাষা।যার মাতৃভাষা নেই,কিবা যার ওপর ভিনদেশী ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়,তার মধ্যে আর বোবা লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য,কোনো তারতম্য থাকে না।সুতরাং- ভাষাটাই মূখ্য।
আমরাই একমাত্র জাতি,ভাষা যে জাতিকে বিশ্বের দরবারে স্বতন্ত্র ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষা রক্ষার আলাপ উঠলেই আমাদের নাম আসে।এটা আমাদের স্বাতন্ত্র্যতা,বৈচিত্র্যতা।আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা।আর বাংলা ভাষায় কথা বলা সকল মানুষের পরিচয় বাঙালি।বাঙালি জাতির বাস এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে তৎকালীন পূর্ব ভারতে।বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গে।ভারত-বাংলাদেশে এই জাতির বাস হলেও ভাষা,ভাষার শান,মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে পূর্ব বঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশীরাই ছিলো সবসময় সোচ্চার।বৃটিশ ভারত হতে ৫২'র ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশীরাই ছিলো ভাষার প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি আপোষহীন।যার দরুন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তরতাজা যুবকদের প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার রক্ষা করতে হয়েছে।
পাক আমলে বাংলা ভাষা আন্দোলনে সাফল্য আসলেও এর বীজ রোপণ ছিলো বৃটিশ ভারতেই।বিশ শতকের গোড়ার দিকে সর্বভারতীয় সচেতন সমাজ একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।তখনো সর্ব ভারতে ফার্সি এবং উর্দু ভাষার আধিপত্য।ততদিনে ইংরেজি ভাষার প্রতিও অনেকেরই ঝোঁক বাড়ে,বিশেষ করে সর্বভারতীয় হিন্দু সমাজে।মূলত সেই অনুভব থেকেই ভারতে রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নের সূত্রপাত।
হিন্দু সচেতন নেতৃত্ব হিন্দি এবং মুসলিম সচেতন নেতৃত্ব উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে আলোচনায় আনে।বিশ শতকের শুরুর দিকে "ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি না উর্দু " এ নিয়ে মোটামুটি তুমুল প্রস্তাব-প্রতিবাদ হয়।তখনো সর্বভারতীয় সকল প্রদেশের সকল ভাষা হতে পূর্ব ভারতের বাংলা ভাষা সকল ভাষাকে ছাড়িয়ে অনন্য উচ্চতায়।মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা বিশেষ ভাবে স্থান পায় বাঙালি মুসলমান সমাজে।পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সমাজ তখনো উত্তর ভারতীয় হিন্দি প্রস্তাবের ওপর বিশ্বস্ত।পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের সাধারণত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কটু ও উদাসীন-ই ছিলো।শুধু বাংলায় কথা বলা হিন্দুদেরকেই তারা বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো।পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা মনে করতো মুসলমানদের হাতে বাংলা ভাষার অধঃপতন হবে।অথচ বঙ্গের মুসলিমরাই বিশ শতকের শুরু হতে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এককভাবে লড়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে যা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বে একমাত্র বাঙালি মুসলমান সমাজই দেখাতে পেরেছে।
বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে প্রথম দাবি উঠে ১৯১১ সালে।তখন সমগ্র ভারতে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন জোড়ালো।ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি নাকি উর্দু হবে এ নিয়ে জোড়ালো আলোচনা চলছিলো।সে সময়ে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি জমিদার পরিবারের নবাব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী রংপুরে একটি প্রাদেশিক অধিবেশনে ১৯১১ সালে প্রথম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরন।বক্তব্য প্রদানকালে এক পর্যায়ে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন- "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা,মাতৃ স্থানের ন্যায়,জন্মভূমির শান্তিনিকেতনের ন্যায় বাংলা ভাষা।বাংলা ভাষা আমাদের নিকট প্রিয়,কিন্তু হতভাগ্য আমরা,মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আমরা উদাসীন।অধঃপতন আমাদের হবে না তো কার হবে?"
এর কিছুকাল পর ১৯১৮ সালে আবার ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন হলে ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে দাবি তুলেন।বিশ্বভারতীতে এক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য দেন।এরপরই ভাষার প্রশ্নে সবচেয়ে যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পুনরায় করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী।১৯২১ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বৃটিশ সরকারের নিকট লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন।১৯২৯ সালে মতিলাল নেহেরু হিন্দি ভাষাকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব পেশ করেন।১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে জয়ী হলে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে জোর কাজ চালায়।মুহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ অপরাপর নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানায়।উর্দু ভাষাভাষী লোকজন উর্দুকে এবং বাংলা ভাষাভাষী লোকজন বাংলা ভাষার পক্ষে জোড়ালো প্রচার চালায়।কংগ্রেসের এই কাজের প্রতিবাদে ১৯৩৭ সালের ২৩শে এপ্রিল দৈনিক আযাদ পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ আকরাম খাঁ পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলে ধরেন।তিনি উল্লেখ করেন- "সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।বাংলা ভাষায় বিবিধভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের সংখ্যাই বেশি।অতএব বাংলা ভাষা সবদিক দিয়েই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবি করিতে পারে।মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছে বটে,কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষার চেয়ে হিন্দির যোগ্যতা কোন দিক দিয়েই বেশি নহে।"
দেশ ভাগের ঘোষণায় সর্ব ভারতীয় রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন হতে আমরা ছিটকে যাই।আমাদের সাথে রয়ে যায় উর্দু ভাষার দাবি।দেশ ভাগের ঘোষণা হতে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর প্রভাব লক্ষ্য করা গেলে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের কান খাড়া হয়ে যায়।পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর প্রতি আনুকূল্য লক্ষ্য করা গেলে পূর্ব পাকিস্তান হতেও বাংলার পক্ষের দাবি সতেজ হয়ে উঠে।১৯৪৩ সালে আবুল মুনসুর আহমেদ মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় "পূর্ব পাকিস্তানের জবান" নামক প্রবন্ধে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার কথা উল্লেখ করেন।১৯৪৬ সালে সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকায় কবি ফররুখ আহমদ রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে জোড়ালো অভিমত তুলে ধরেন।"পাকিস্তান: রাষ্ট্র ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদ বলেন- "গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হওয়া উচিত,সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাকে পর্যন্ত যারা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তর করতে চান তাদের উদ্দেশ্য অসৎ।পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"
৪৭'র জুন-জুলাইয়ে আব্দুল হক পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।৪৭'র জুনের ৩০ তারিখে দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা" নামক প্রবন্ধে বলেন- "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হবে তা এখন স্থীর করার সময় এসেছে।যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ করি,তার আগে আমাদের বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হবে।....কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক কথা বলে,পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি,কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন ভাষা ভাব প্রকাশে সব থেকে বেশী উপযোগী।...যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন,পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশি।"
দেশ ভাগের অল্প প্রাক্কালে জুলাইয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নটি নতুন করে উসকে দেয় আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ।সেকেন্দ্রবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।এর প্রতিবাদে ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ দৈনিক আজাদী পত্রিকায় "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা" প্রবন্ধে বলেন- কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমই হইবে।... ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে,ইহা পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়।উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন,যেমন- পশতু,বেলুচি,পাঞ্জাবি,সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলেই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়।যদি বিদেশি ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়,তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্র ভাষা গ্রহণ করতে হয়,তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।"
এছাড়াও এসময়ে মাহবুব জামাল জাহেদী,ড. এনামুল হকসহ আরো অনেকেরই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্বারোপ করেন।জাহেদী ও ড.হক পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দু এবং বাংলা দুটি ভাষারই প্রস্তাব করেন।
দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন সচেতন শিক্ষিত সমাজ,বুদ্ধিজীবী,সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।দেশভাগের পরপরই ভাষা আন্দোলনকে একটি জন সম্পৃক্ত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ দেয় তমদ্দুন মজলিশ।তমদ্দুন মজলিসই একমাত্র সংগঠন যারা প্রথম সাংগঠনিক ভাবে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে।২০২০ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা'র শীত সংখ্যায় "বাংলা ভাষা আন্দোলন: বায়ান্ন-পূ্র্ব পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এম. মুনজুরুল হক বলেন- "ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।বাংলা ভাষার দাবিতে প্রথম " রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" মজলিশের উদ্যোগেই গঠিত।ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারেও ওই সংগঠনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।"
ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ভাব সমুন্নত রাখতে ইসলামি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ৪৭'র ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।মুসলমানদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন পালনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজ ও অধ্যাপকদের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ আত্মপ্রকাশ করে এবং সংগঠনটি একই সাথে পূর্ব বাংলার আপামর মানুষের মুখের ভাষার তাৎপর্যের বিষয়টি সামনে রেখে দেশ ভাগের পরপরই রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে জোড়ালো অবস্থান গ্রহণ করে।এর নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম।
১৫ই সেপ্টেম্বর "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু" শিরোনামে তমদ্দুন মজলিশ সর্বপ্রথম একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের সবগুলোতেই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।পুস্তিকাটিতে প্রবন্ধ লিখেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন,আবুল মুনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাশেম।
কাজী মোতাহার হোসেন পুস্তিকায় "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন- "বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়,সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না।তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নাতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকদের কর্তব্য।"
"বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল মুনসুর আহমদ বলেন- "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকুরীর অযোগ্য বনিয়া যাইবেন।উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।"
পুস্তিকাটির প্রথমেই সংগঠনটির পক্ষ হতে রাষ্ট্র ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব লিখেন অধ্যাপক আবুল কাশেম।প্রস্তাবনাটির প্রথমাংশে বলা হয়-
১. বাংলা ভাষাই হবে: (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন (খ) পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা (গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।
২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি- উর্দু ও বাংলা।
উল্লেখ্য বিষয় যে,রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষের ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে শুধুমাত্র বাংলার কথা কখনো বলেননি।তারা বাংলার পাশাপাশি উর্দুকেও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন।কিন্তু শাসক গোষ্ঠী গোটা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষের ভাষার পরিবর্তে শুধুমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রস্তাব আনে।অথচ উর্দু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অংশের তো নয়-ই,এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত অংশেরও মুখের ভাষা ছিলো না।
৪৮'র মার্চে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ জেগে ওঠে।রেসকোর্স ও কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ'র এই প্রস্তাবের সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ছাত্র সমাজ।ততদিনে দেশের অন্যান্য শহরগুলোতেও ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় করাচিতে।প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন।প্রস্তাবটি মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের বিরোধিতার মুখে বাতিল করা হয়।ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির প্রতিবাদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন- "পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।"
গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় বাংলা ভাষাভাষী সদস্যরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার খবর পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে গেলে দেশজুড়ে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।বাংলা ভাষার পক্ষের পত্রিকা নওবেলাল,দৈনিক আজাদ,দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদকীয়তে লিয়াকত আলীর বক্তব্যের তুলোধুনো করে।কলকাতা হতে প্রকাশিত আনন্দবাজার,অমৃতবাজার ও স্বাধীনতা তাদের সম্পাদকীয়তে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে সম্পাদকীয় লিখে।গণ পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের বিরোধিতায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়।রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার আত্মমর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলে কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সভায় শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।মূলত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের স্ফুরণ ঘটানোর পথ সুগম হয়।এই দিনেই ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।৪ঠা আগস্ট সিলেটের নওবেলাল সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষার পক্ষে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।পরবর্তীতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনে উগ্রবাদী উর্দু সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েন নও বেলাল সম্পাদক মুহাম্মদ আজরফ এবং আহত হোন।
ভাষা আন্দোলনে ঢাকার বাহিরে সিলেটের ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য।আন্দোলনের শুরু হতেই সিলেটে সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ করার মতো।নও বেলাল পত্রিকার ভূমিকা ছিলো প্রথম সারিতে।১১ই মার্চ সিলেটের ১৮জন বিশিষ্ট নাগরিকের যৌথ বিবৃতি ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ভাষা আন্দোলনে ৪৮'র ১১ই মার্চ ছিলো টার্নিং পয়েন্ট।দেশ ভাগের পর পাকিস্তানে এটাই প্রথম জোড়ালো আন্দোলন।১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনে বহু ছাত্র,সাংস্কৃতিক কর্মী ও রাজনীতিক নেতা-কর্মীদের পুলিশ গ্রেফতার করে।পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ছাত্র,শিক্ষক,পেশাজীবি,বুদ্ধিজীবীসহ অনেকেই আহত হোন।এর প্রতিবাদে পরবর্তী তিন দিন যথাক্রমে ১২,১৩ ও ১৪ই মার্চ পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়।১১ই মার্চে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের আক্রমণের ফলে আন্দোলন তীব্র দানা বাঁধতে শুরু করে এবং ১৭ই মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন চলে।১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন মাওলানা ভাসানী,ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত,আবু তায়েব মাজহারুল হক,মাহমুদ আলী,মনোরঞ্জন ধর,শামসুদ্দিন আহমেদ,মহিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আন্দোলনের চাপে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি মেনে নিয়ে রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদের নেতাদের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।১৭ই মার্চ অধিবেশনে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান মওলানা ভাসানী।জিন্নাহ পুনরায় ঢাকায় এসে বাংলা ভাষার প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন এই ধারণায় ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলের হাউস টিউটর মাজহারুল হকের রুমে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।ভাষার প্রশ্নে আপোষহীন থাকায় সরকার কর্তৃক মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে চাপ প্রয়োগ করা হলে স্বেচ্ছায় তিনি আন্দোলন প্রশ্নে ব্যবস্থাপক সদস্য পদ হতে পদত্যাগ করেন।
বাংলা ভাষার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য পরিষদও বেশ জোড়ালো অবস্থান গ্রহণ করে।৪৮'র ৩১ শে জানুয়ারী এবং ৪৯'র ১লা জানুয়ারি সংগঠনটির সাহিত্য সম্মেলনে বেশ জোড়ালো ভাবে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবি উত্থাপন করা হয়।১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক সরকার বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন,সহজিকরণ ও সংস্কারের বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ কে সভাপতি ও গোলাম মোস্তফাকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি "ভাষা কমিটি" গঠন করে।বাংলা ভাষার কিছু পরিবর্তন এনে "সহজ বাংলা" নামে একটি প্রস্তাবনায় আরবি ও ফার্সি বর্ণমালায় বাংলা লেখার জন্য ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করে।যা সকলে প্রত্যাখ্যান করে।
৫০'র দশকে কবি গোলাম মোস্তফা "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ভাষা: উর্দু না বাংলা", সৈয়দ মুজতবা আলী " পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা শীর্ষক" নামক দুটি প্রবন্ধ লিখে।প্রথম প্রবন্ধটিতে গোলাম মোস্তফা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে,এবং ঐক্য,সংহতি ও ইসলামের স্বার্থে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই জোরালো মত দেন।এর প্রেক্ষিতে সৈয়দ মুজতবা আলী গোলাম মোস্তফার সকল যুক্তি পেছনে ফেলে ভাষা হিসেবে উর্দু হতে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের বক্তব্য তুলে ধরেন।তার আলোচনায় শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার কথা বললেও,সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কি হবে এবিষয়ে কিছু বলেননি।
৪৮'র ১৫ই মার্চ নাজিমুদ্দিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন না হলে পরবর্তীতে নুরুল আমিন সরকারের সময়ে ১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব শ্রেণির সমন্বয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।স্বারক লিপিতে ১লা এপ্রিল হতে সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রচলন শুরুর কথা বলা হয়।১৯৫১ সালে মার্চ মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কঠোর সমালোচনা করে জোরালো ভাবে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে দাবি উত্থাপন করা হয়।১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান উর্দু সম্মেলনে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার দাবিদারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র,শিক্ষক,জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানের জনসভায় রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে আবারো উর্দুর ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন নতুন করে ফুঁসে উঠে।প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই দিনই বিকেলে ভাসানীর নেতৃত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে ৫২'র ৩০শে জানুয়ারি হতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সভা,সমাবেশ,মিছিল,মিটিং ও ধর্মঘট চলতে থাকে।২১শে ফেব্রুয়ারী ছিলো পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন।এই দিনটিকে আন্দোলনকারীরা গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করে।পরিকল্পনা মতে অধিবেশনর স্থান জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে গিয়ে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।ঢাকা সহ সমস্ত দেশে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়।বিপরীতে সরকার ১৪৪ দ্বারা জারি করলে আন্দোলনকারীরা ১৪৪ দ্বারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে।আন্দোলন দমাতে নুরুল আমিন সরকারের নির্দেশে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালে রফিক,শফিক,জব্বারসহ আরো অনেকের বুক ঝাঁঝরা হয়।পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।
ঘটনার এখানেই শেষ নয়।২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীদের হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশ ২২ ও ২৩ শে ফেব্রুয়ারী হরতাল ডাকা হয়। ২৩ তারিখে বিকেলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে শহিদদের স্বরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।২৬ শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ স্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দেয়।প্রথমটি ভেঙে ফেলা হলে পুনরায় আরো একটি শহিদ স্তম্ভ নির্মাণ করা হলে সেটিও সরকারের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়।বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা,শিক্ষক,লেখক,বুদ্ধিজীবী আন্দোলন চালিয়ে রাখে।একপর্যায়ে ক্রমাগত আন্দোলনের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।৫২ সালে রক্ত ঝরার স্বীকৃতি ৫৪ হয়ে ৫৬ সালে মর্যাদায় ভূষিত হয়।রক্ষা হয় মায়ের ভাষা,প্রাণের ভাষা বাংলার সম্মান।৫৪ হয়ে ৫৬ তে স্বীকৃতি পেলেও ভাষা আন্দোলনে গুরুত্ব পায় ৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি।কারণ সেদিনই ভাষার জন্য শুধু রক্ত নয়,প্রাণও ঝরে ছিলো।তখন হতেই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা দিবস বা শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে পূর্ব বঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের আপামর জনতা।পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে পাক শাসনাধীন হতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা মর্যাদা লাভ করে এবং ভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাভাষীদের অক্লান্ত এই আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।যা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে তুলে।ঢাকায় প্রথম নির্মিত দুটি শহিদ মিনার পুলিশ ভেঙে দিলে ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বর্তমান স্মৃতি স্তম্ভ বা শহিদ মিনারটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।এর নকশাকার ছিলেন স্থপতি হামিদুর রহমান। প্রথমটির নকশা করেছিলেন বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার।
Copyright © 2025 cetonaibangladesh.news. All rights reserved.